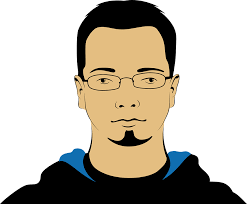

এসব সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলো প্রায়শই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গা শিউরানো ভিডিও বা যেসব ভিডিওতে অত্যাচার নির্যাতনের অস্বস্তিকর ছবি আছে সেগুলো সরিয়ে নেয়। কিন্তু তারা বলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজ মামলা দায়েরে সহায়তা করতে পারে সেগুলো আর্কাইভে সংরক্ষণ না করে নামিয়ে নেয়া সম্ভব।
মেটা এবং ইউটিউব বলছে, এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য হল একদিকে কোন কিছুর সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরা এবং অন্যদিকে ক্ষতিকর কন্টেন্ট থেকে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা।
তবে মেটার ওভারসাইট বোর্ড, যারা মেটা মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর সার্বিক নজরদারি করে তার সদস্য অ্যালান রাসব্রিজার বলছেন, এই খাতের কোম্পানিগুলো কন্টেন্ট নজরদারির ক্ষেত্রে “প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর্ক”।
এই প্ল্যাটফর্মগুলো বলছে, এধরনের কোন কন্টেন্ট যদি জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে সেগুলো সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা তাদের আছে। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধে বেসামরিক মানুষের ওপর হামলার নথিসম্বলিত ফুটেজ বাংলার মুখ বিডি ২৪ আপলোড করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছে সেগুলো খুব দ্রুত সরিয়ে নেয়া হয়েছে।
আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাধারণভাবে ক্ষতিকর এবং অবৈধ কন্টেন্ট সরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যখন যুদ্ধের সহিংস ফুটেজ নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয়, তখন কোনটা মানবাধিকার লংঘন বলে গণ্য হতে পারে, সেই সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা তার থাকে না।
মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে এসব তথ্য যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য সোশাল মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।
“প্ল্যাটফর্মগুলোতে অসহনীয় বা মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে এমন কিছু দেখার সাথে সাথেই সেগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য কোম্পানিগুলো কেন যান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করছে এবং তাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সেটা বোধগম্য,” বাংলার মুখ বিডি ২৪কে বলেছেন মি. রাসব্রিজার। যে সার্বিক নজরদারি বোর্ডের তিনি সদস্য, সেই বোর্ড চালু করেছিলেন মার্ক জাকারবার্গ এবং তার কোম্পানি, যা ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মালিক, সেই কোম্পানির জন্য এই বোর্ড এক ধরনের নিরপেক্ষ “সুপ্রিম কোর্ট” হিসাবে পরিচিত।
“আমি মনে করি এখন তাদের ভাবতে হবে এমন একটা ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব – সেটা মানুষ বা এআই প্রযুক্তি যেটা ব্যবহার করেই হোক না কেন – যে ব্যবস্থা আরও যুক্তিসঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে,” আরও বলেন মি. রাসব্রিজার, যিনি গার্ডিয়ানের সাবেক প্রধান সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সামাজিক মাধ্যমে কন্টেন্টের ওপর নজরদারির অধিকার যে রয়েছে, তা কেউ অস্বীকার করছে না, বলছেন গ্লোবাল ক্রিমিনাল জাস্টিসের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বেথ ভ্যান শ্যাক: “আমার মতে, উদ্বেগের কারণ ঘটছে, যখন সেই তথ্য বা কন্টেন্ট হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যাচ্ছে।”
সাবেক এক পর্যটন সাংবাদিক ইহর জাখারেঙ্কোর সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে ইউক্রেনে। সেখানে রাশিয়া আক্রমণ চালানোর পর থেকে তিনি বেসামরিক মানুষদের ওপর হামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ নথিবদ্ধ করছেন।
কিয়েভের এক শহরতলিতে তার সঙ্গে দেখা করে বাংলার মুখ বিডি ২৪। সেখানে রুশ দখলীকৃত এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টার সময় এক বছর আগে পুরুষ, নারী ও শিশুদের রুশ সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে।
তিনি সেখানে অন্তত ১৭টি মৃতদেহের এবং অগ্নিদগ্ধ গাড়ির ভিডিও ছবি তোলেন।
তিনি এসব ভিডিও অনলাইনে পোস্ট করতে চেয়েছিলেন যাতে বিশ্বের মানুষ দেখতে পায় কী হচ্ছে এবং ক্রেমলিনের বক্তব্যকে তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু তিনি ওইসব ফুটেজ ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়।
“রাশিয়ানরা বলছিল ওগুলো ভুয়া। তারা কোন বেসামরিক মানুষের গায়ে হাত দেয়নি, তারা শুধু ইউক্রেনীয় সৈন্যদের সঙ্গে লড়ছে,” জানান ইহর।
বাংলার মুখ বিডি ২৪নতুন বিকল্প অ্যাকাউন্ট খুলে ইহরের ফুটেজগুলো ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবে আপলোড করে।
চারটির মধ্যে তিনটি ভিডিও, ইনস্টাগ্রাম এক মিনিটের মধ্যে সরিয়ে নেয়।
ইউটিউব প্রথমে ওই একই তিনটি ভিডিও দেখার ওপর বয়সসীমা আরোপ করে, কিন্তু পরে ১০ মিনিটের মধ্যে সবগুলো ভিডিওই তারা সরিয়ে ফেলে।
আমরা আবার ভিডিওগুলো আপলোড করার চেষ্টা করি – কিন্তু সেগুলো আর তোলা যায়নি। ভিডিওগুলোতে যুদ্ধাপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, সেই যুক্তিতে ওগুলো পুনরুদ্ধারের দাবি জানালে সে দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হয়।
ইউটিউব এবং মেটার বক্তব্য অনুযায়ী, যেসব কন্টেন্ট সাধারণভাবে সরিয়ে নেয়ার নীতি আছে, কিন্তু যুদ্ধের বিশদ ফুটেজের কারণে যেগুলো জনস্বার্থে রাখা জরুরি, সেগুলো না সরানোর বিধান রয়েছে, এবং শুধু প্রাপ্তবয়স্করা দেখতে পারবেন সেগুলো এই নিয়ম অনুযায়ী রাখার কথা। কিন্তু ইহরের ভিডিও নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে এই নীতি কাজ করে না।
মেটা বলছে তাদের পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে “বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ন্যায্য আইনি অনুরোধ” এবং “আইন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার আর আন্তর্জাতিক স্তরে দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানাতে আরও কী পথ আছে তার জন্য আমাদের অব্যাহত অনুসন্ধান।”
ইউটিউব বলছে নাড়া দেয়া জ্বলন্ত দৃষ্টান্তমূলক কন্টেন্ট জন স্বার্থে মুছে না ফেলার নীতি তাদের থাকলেও, “ইউটিউব কোন আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা নয়। মানবাধিকার সংগঠন, আন্দোলনকর্মী, মানবাধিকার প্রবক্তা বা মানবাধিকারের পক্ষে যারা লড়াই করছেন, গবেষক, সাংবাদিক নাগরিক, অথবা যারা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা নথিবদ্ধ করেন কিংবা সম্ভাব্য অপরাধ খতিয়ে দেখেন, তাদের কাজের কারণে কন্টেন্ট সংরক্ষণ বা সেগুলো নিরাপদে রাখার সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করা তাদেরই দায়িত্ব।”
বাংলার মুখ বিডি ২৪ আরও কথা বলেছে ইমাদের সাথে। সিরিয়ায় আলেপ্পোর কাছে ২০১৩ সালে সিরিয়া সরকার ব্যারেল বোমা হামলা চালানোর আগ পর্যন্ত অ্যালেপ্পোয় তার একটা ওষুধের দোকান ছিল।
তার মনে আছে ওই বোমা হামলায় ঘরের ভেতর ধুলো আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে সাহায্যের জন্য মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে তিনি বাইরে বাজার এলাকায় গিয়ে দেখেছিলেন পড়ে আছে মানুষের রক্তাক্ত লাশ, ছিন্নভিন্ন হাতপা।
স্থানীয় টিভি সাংবাদিকরা এসব দৃশ্যের ছবি তুলেছিলেন। ফুটেজ পোস্ট করেছিলেন ইউটিউব আর ফেসবুকে। কিন্তু পরে সেগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়।
সিরিয় সাংবাদিকরা বাংলার মুখ বিডি ২৪কে বলেন যুদ্ধের ডামাডোলে, বোমা হামলায় তাদের নিজেদের তোলা ভিডিও ফুটেজও ধ্বংস হয়ে গেছে।
যুদ্ধের কয়েক বছর পর ইমাদ যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আশ্রয়ের আবেদন করেন, তাকে বলা হয় তিনি যে ঘটনাস্থলে ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ নথি দেখাতে হবে।
“আমি নিশ্চিত আমার ওষুধের দোকানের অবস্থা ক্যামেরায় ধরা ছিল। কিন্তু আমি যখন অনলাইনে খোঁজ করলাম আমাকে দেখানো হল সংশ্লিষ্ট ভিডিও ‘ডিলিট’ করে দেয়া হয়েছে।”
এধরনের অভিজ্ঞতার আলোকে নেমোনিক নামে বার্লিন ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা এই ধরনের কন্টেন্ট সরিয়ে নেয়ার আগেই তা আর্কাইভ করার কাজে এগিয়ে এসেছে।
তারা এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছে যা মানবাধিকার লংঘনের সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বলিত কন্টেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করে সেভ করে রাখছে। প্রথমে সিরিয়ার কন্টেন্ট তারা সংগ্রহ করেছে, এরপর এখন কাজ করছে ইয়েমেন, সুদান আর ইউক্রেনের ফুটেজ নিয়ে।
সামাজিক মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলার আগেই তারা যুদ্ধ এলাকার সাত লাখের ওপর ছবি সেভ করে রেখেছে। এর মধ্যে ইমাদের ওষুধের দোকানের কাছে হামলার তিনটি ভিডিও রয়েছে।
এধরনের প্রতিটি ছবির মধ্যে হয়তো এমন গুরুত্বপূর্ণ সূত্র রয়েছে যা ধরে বের করা সম্ভব রণাঙ্গনে বা হামলার জায়গায় ঠিক কী ঘটেছিল- ঘটনাস্থল, তারিখ এমনকী হামলাকারীরও হদিশ মিলতে পারে।
তবে নেমোনিক-এর মত সংগঠনগুলোর পক্ষে সারা বিশ্বের প্রতিটি সংঘাতস্থলের ছবি বা ভিডিও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।
যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। কাজেই যত বেশি সম্ভব সূত্র পাওয়াটা এজন্য জরুরি।
“যাচাই প্রক্রিয়া অনেকটা ধাঁধাঁ সমাধান করার মত- কী হয়েছিল তার সঠিক ধারণা পেতে হলে কার্যত সম্পর্কহীন বিভিন্ন তথ্যও আপনাকে জোড়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র খোঁজার চেষ্টা করতে হবে,” বলছেন ‘বাংলার মুখ বিডি ২৪ ভেরিফাই’ বিভাগের অলগা রবিনসন।
সামাজিক মাধ্যমে অজানা সূত্র থেকে প্রায় সকলের কাছেই নানা তথ্য আসে। সহিংস সংঘাতে জড়িয়ে পড়া আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করতে যারা উদ্যোগী হন অনেক সময় এসব তথ্য ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করার কাজটা তাদের ঘাড়েই পড়ে।
রাহোয়া থাকেন আমেরিকায় এবং তার পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন ইথিওপিয়ার টিগ্রে এলাকায়। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ব্যাপক সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকা। সেখানে ইথিওপিয়ার কর্তৃপক্ষ তথ্যপ্রবাহ কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে।
তবে সোশাল মিডিয়ার দৌলতে সংঘাতের দৃশ্যমান রেকর্ড এখন দুর্লভ নয়। আগে এসব ঘটনা বিশ্ববাসীর চোখের আড়ালেই থেকে যেত।
“এটা আমাদের কর্তব্য,” রাহোয়া বলেন। “আমি এনিয়ে বহু ঘণ্টা গবেষণার কাজ করেছি। কাজেই এধরনের কন্টেন্ট দেখলে যেসব গোয়েন্দা তথ্য আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত সূত্র থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব, সেসব তথ্যের আলোকে এগুলো যাচাই করার চেষ্টা আপনি সহজেই করতে পারেন। অবশ্য আমার পরিবার ঠিক আছে কিনা সেটা আমি জানব না।”
মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা কন্টেন্ট সংগ্রহ করার এবং সেগুলো নিরাপদ স্থানে মজুত রাখার জন্য একটা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলা খুবই জরুরি। কন্টেন্টের তথ্য বা মেটাডেটা সংরক্ষণের বিষয়টা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই দরকার, যাতে এসব কন্টেন্ট যাচাই করে দেখা যায়, কোথায়, কখন, কীভাবে এসব ছবি বা ভিডিও তোলা হয়েছিল এবং এসব তথ্যের কেউ ইচ্ছা করে কোনরকম রদবদল করেনি।
গ্লোবাল ক্রিমিনাল জাস্টিসের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিজ ভ্যান শ্যাক বলছেন: “আমাদের এমন একটা পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এগুলোর সম্ভাব্য বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রমাণযোগ্য তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে আগ্রহী হতে হবে।”